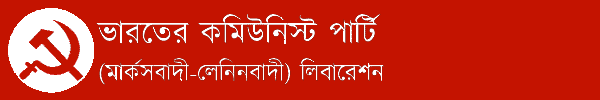আঠারো শতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ইংরেজদের কাছে চলে গেলেও প্রথমদিকে ভারতীয় বা বাঙালি সমাজের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার তেমন প্রভাব পড়েনি। এই প্রভাব পড়তে শুরু করে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। একদিকে রামমোহনের মতো ব্যক্তিত্বের কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৮১৫ সাল) ও অন্যদিকে হিন্দু স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার (১৮১৭ সাল) সূত্র ধরে এই প্রভাব পড়া শুরু হয়। বাঙালি সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব প্রথমদিকে খুব অল্প লোকের মধ্যেই পড়েছিল কিন্তু সেই প্রভাবের অভিঘাত ছিল বেশ গভীর। ১৮৩০ সালের মধ্যেই হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও ও নব্য প্রচলিত পাশাচত্য শিক্ষার হাত ধরে আসা যুক্তিবাদকে ঘিরে ডিরোজিয়ানদের কার্যকলাপ সমাজে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। রামমোহন যখন সতীদাহর মতো নির্মম প্রথা রদ করার আন্দোলনে নামলেন তখন হিন্দু সমাজের ভেতরের রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। এই প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভবানীচরণ সম্পাদিত সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকার লেখাগুলি পড়লে। কলিকাতা কমলাললয়, নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস ভবানীচরণের লেখা এই বইগুলিতেও ইয়ং বেঙ্গলদের বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ রয়েছে।
পরিবর্তন ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বের এই প্রেক্ষাপটে বাবা ঠাকুরদাসের হাত ধরে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কোলকাতায় হেঁটে আসেন ন’বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র, পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনো করে যিনি বিদ্যাসাগর উপাধি পাবেন। বিদ্যাসাগরকে তাঁর বাবা কোলকাতায় পড়াশুনোর জন্য নিয়ে এলেন ঠিকই কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলদের নিয়ে তপ্ত হয়ে থাকা হিন্দু স্কুলের পরিবর্তেতাঁকে পড়ানো হল সংস্কৃত কলেজে। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্য কাব্য দর্শনে পণ্ডিত হয়ে উঠলেও পরবর্তীকালে শিক্ষানীতি নিয়ে কথা বলার সময় অদ্বৈত বেদান্ত বা নব্যন্যায় বা সাংখ্যকে পাঠ্য তালিকায় আর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাখতে চাননি। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্বে বাঙলার শিক্ষাজগৎ আলোড়িত ছিল প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের দ্বন্দ্বে। অ্যাডামস রিপোর্ট, উডের ডেসপ্যাচ, মেকলের মিনিট ও অসংখ্য বিতর্ক পেরিয়ে যখন পাঠশালা বা মক্তবের বদলে শেষমেষ পাশ্চাত্য ধরনের স্কুল সিস্টেমকেই এদেশের শিক্ষার কাঠামো হিসেবে বেছে নিয়ে নতুন নতুন স্কুল স্থাপণ করা শুরু করল কোম্পানির শাসন, তখন শিক্ষা প্রশাসকেরা বিদ্যাসাগরকে এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে বাংলার নানা প্রান্তে নতুন নতুন স্কুল তৈরি ও তার মানোন্নয়নে নিজের প্রাণশক্তি উজাড় করে দিলেন। বিশেষ জোর দিলেন মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে। যে মেয়েরা এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেই মূলত অবস্থান করত, তাদের বাংলার শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের ভূমিকা অসামান্য। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে একই ধরনের প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করছিলেন জ্যোতিরাও ফুলে ও সাবিত্রী ফুলে।
(ফুলেদের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী পাঠকেরা পড়তে পারেন মলয় তেওয়ারির লেখা এই নিবন্ধটি https://www.itihasadda. in/savitribai-phule/)
কোম্পানির শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তারকের এই ভূমিকা বাঙালি সমাজে তাঁর সম্মানের চিরন্তন আসনের অন্যতম কারণ। আবার ঔপনিবেশিক শাসকের এই সহযোগী ভূমিকার জন্যই অনেকে তাঁর প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছেন। অনেকে এও মনে করেছেন অ্যাডামস রিপোর্ট থেকে নাকি জানা যায় বাংলার তৃণমূলস্তরে পাঠশালা মক্তবের এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ছিল, আর সেটাই নাকি ছিল বুনিয়াদী গণশিক্ষা ও দেশজ সংস্কৃতির জন্য যথার্থ। তাঁদের মতে বিদ্যাসাগর প্রমুখদের এই নয়া শিক্ষা কার্যক্রম আমাদের দেশীয় শিক্ষার ধারাকে অস্বীকার করেছে, তাকে সমাজের অল্প কিছু মানুষের জন্যই কেবল উন্মুক্ত করেছে এবং তার মূল লক্ষ্য থেকেছে কোম্পানির প্রশাসনের জন্য কেরানি তৈরি করা। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিতর্কে প্রবেশ করার সুযোগ খুবই কম। কেবল এটুকু বলার উত্তর ঔপনিবেশিক অবস্থানভূমি থেকে এই সমালোচনা অনেক সময়েই তথ্যর আংশিকতা ও স্বকপোলকল্পিত যুক্তিবিন্যাস-এ আবদ্ধ। অন্যান্য সূত্র ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অ্যাডামস রিপোর্ট প্রথমে যে একলক্ষ পাঠশালা মক্তবের বিস্তারিত নেটওয়ার্ক এর কথা বলেছিল তা ছিল একটি আনুমানিক ও ভুল তথ্যসংগ্রহ। অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে তা সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তার সংখ্যা ছিল অনেক অনেক কম। দ্বিতীয়ত এগুলিতে মেয়েদের পড়াশুনোর কোনও বালাই ছিলনা। তৃতীয়ত এখানে যা পড়ানো হত ও যেভাবে পড়ানো হত তা ‘কেরানি তৈরির পাশ্চাত্য শিক্ষা’র পাঠ্যক্রমের তুলনাতেও ছিল নিতান্ত সাদামাটা এবং তাতে মৌলিক জীবনভাবনার বিকাশ ও বিজ্ঞান বা সাহিত্যের আধুনিক বা ধ্রুপদী কোনও কিছুর সাথেই কোনওরকম পরিচয়ের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ধরমপাল প্রমুখরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা নিয়ে যে কাজ করেছেন তা আমরা দেখেছি। সেখানেও রাজা-রাজড়াদের কিছু মানমন্দির স্থাপণের বাইরে উন্নত গণশিক্ষার কোনও হদিশ পাইনি।
(আগ্রহী পাঠকে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন ধরম পালের লেখা “The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century” বইটি)
ফলে কোম্পানি শাসনে বাংলার কৃষি কারিগরী ধ্বংস ও অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে যারা দেশীয় শিক্ষার কাঠামো ধ্বংসের অভিযোগকে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলেন ও বিদ্যাসাগর প্রমুখকে অভিযুক্ত করেন – তাদের একদেশদর্শী তথ্য উপস্থাপণ ও যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে একমত হওয়ার কোনওরকম কারণ আমরা খুঁজে পাই না। এবার চলে আসা যাক শিক্ষা সংস্কারক বিদ্যাসাগরের পাঠ্য বই লেখার দিকটিতে। বিদ্যাসাগর যখন ছোটদের জন্য পাঠ্যবই লেখার কাজ শুরু করলেন তখনো বাংলা গদ্য সাহিত্য যথেষ্ট বিকশিত নয়। ঊনিশ শতকের আগে বাংলায় গদ্যের ব্যবহারের নিদর্শন বলতে ছিল কিছু চিঠিপত্র, কড়চা আর মানোএল দা আসসুম্পাসাঁও বা দোম আন্তোনিওদের মতো পর্তুগীজ উদ্যোগে রোমান হরফে লেখা বাংলা। ইংরেজ সিভিলিয়ান ছাত্রদের বাংলা শেখানোর জন্য যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি হয়েছিল তার লেখকেরা যেমন রামরাম বসু, মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী যে ধরনের গদ্য লিখছিলেন তাতে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক অন্বয় অনেক সময়েই ঠিকমতো রক্ষিত হয়নি। রামমোহনের গদ্য এই সমস্যামুক্তির প্রথম সার্থক উদাহরণ, তবে গদ্যশিল্প বলতে যা বোঝায় তার বিকাশ বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই হয়েছিল। বিদ্যাসাগর একদিকে সংস্কৃত, হিন্দি বা ইংরাজি সাহিত্য থেকে অনুবাদ ও অনুসৃজন করলেন, অন্যদিকে লিখলেন স্বাধীন মৌলিক গদ্য। বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো বইগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির শিশুশিক্ষার প্রধান অবলম্বন হয়ে থেকেছে।
এই সমস্ত গদ্যগ্রন্থগুলি বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে যেমন স্মরণীয়, তেমনি এগুলির পেছনে বিদ্যাসাগরের যে চিন্তা-চেতনা কাজ করেছে, তা শিশুশিক্ষার সেক্যুলার দিকটিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছে। এই সমস্ত বইগুলিতে নীতিশিক্ষা রয়েছে কিন্তু তা এসেছে ঈশ্বর বা দৈব বিবর্জিত সামাজিক অনুষঙ্গ হিসেবে। বিদ্যাসাগরের এই বইগুলিতে ঈশ্বরচিন্তার অনুপস্থিতির জন্যই জন মার্ডকের মতো অনেকে সেকালে তার সমালোচনা করেছিলেন এবং এগুলিকে মিশনারী স্কুলের পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দেবার জন্য রীতিমতো আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন স্বপন বসুর লেখা বই “সমকালে বিদ্যাসাগর” এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সংবর্তক প্রকাশিত বিদ্যাসাগর জন্ম দ্বিশতবর্ষ সংখ্যায় লেখা প্রবন্ধ “বিদ্যাসাগরের চূড়ান্ত বস্তুবাদ আর না ধর্মীয় ভাব”)
বিদ্যাসাগরের গদ্যের আরেকটি দিক বিকশিত হয়েছিল তার সামাজিক আন্দোলনের সূত্র ধরে। এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে আমরা রামমোহনের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করি। রামমোহনের মতোই বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্রকে তাঁর প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলনের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রামমোহন যেভাবে শাস্ত্র উদ্ধৃত করে সতীদাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরও তাই করেছেন বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বা বহুবিবাহ ও বাল্য বিধবার বিরুদ্ধে। তবে রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলন নিয়ে যে রকম আগ্রহ বোধ করেছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখালেখি করলেও বিদ্যাসাগর সারাজীবনে কখনোই কোনও ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে আগ্রহ ব্যক্ত করেননি। বরং অক্ষয় দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী সামাজিক জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল বলেই বিদ্যাসাগর এই পত্রিকাকে তাঁর লেখালেখির জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই সেক্যুলার মনন একালের ধর্মকেন্দ্রিক উন্মাদনার বাড়াবাড়ির যুগে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখার।
বিদ্যাসাগরের গদ্য সংস্কৃত ভাষার প্রতি বেশিমাত্রায় অনুগত – এমন অভিযোগ অনেকে তুলেছেন। এই সমালোচকদের মাথায় রাখা দরকার বাংলা গদ্যের কাঠামো বিকাশের সেই ঊষালগ্নে বিদ্যাসাগরকে একটি সুবিকশিত গদ্যভাষার আদলকে মাথায় রাখতে হচ্ছিল এবং সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে তাঁর স্বাভাবিক পারঙ্গমতার জন্য এই ভাষার আদলের ব্যবহারই তাঁর কাছে অনায়াস ও স্বাভাবিক ছিল। তিনি রামমোহনের মতো আরবী ফারসী জানতেন না। পরে বিদ্যাসাগর ইংরাজি ভাষা সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং ইংরাজি গদ্যের ছেদ ও যতি চিহ্নকে নিয়ে আসেন বাংলা গদ্যের মধ্যে। বাংলার সমকালীন অন্যান্য গদ্যকারদের মতো সংস্কৃত যতিচিহ্নের অভ্যস্ত পথে আটকে থাকার কোনও লক্ষণই তিনি দেখাননি। বিদ্যাসাগর যখন পরিণত বয়েসে ছদ্মনামে লঘুচরিত্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি লিখেছিলেন, তখন সেখানে বিষয়ের স্বার্থেই সংস্কৃত অনুগ বাংলার পরিবর্তেতিনি অন্য ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গদ্যের স্টাইলিস্টিকস-এর বিশ্লেষণ নির্ভর স্বতন্ত্র এক অনুসন্ধানের জন্যই রাখা থাকল।
বিদ্যাসাগর যে সময়ে সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁকে ও অন্যান্যদের কাজ করতে হয়েছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। সেই ঔপনিবেশিক কাঠামো এদেশকে শাসন শোষণ করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। এদেশের পুরনো অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ধ্বংস ও লুঠ করে তারা এদেশের সম্পদকে নিজেদের দেশে শিল্পায়নে কাজে লাগিয়েছিল, কিন্তু এদেশে কোনও শিল্পায়ন বা উন্নয়নের চেষ্টা করেনি। ফলে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যে রেনেসাঁ সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার কারণে, এদেশে সেই অর্থে তার কোনও সার্বিক সাফল্য সম্ভাবনা ছিল না। কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার সে কালের বিশিষ্টরা সম্ভব করে তুলতে পারলেও বড় ধরনের কোনও সমাজ জোড়া আমূল পরিবর্তন ঊনিশ শতকের বাংলায় সম্ভব ছিল না। এই সীমাবদ্ধতা বিদ্যাসাগর বা তাঁর সমকালীন অন্যান্য বিশিষ্টদের ব্যক্তিগত কোনও সীমাবদ্ধতা নয়, বস্তুগত পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা। বিদ্যাসাগর সহ ঊনিশ শতকের বিশিষ্টদের মূল্যায়নের সময় এটা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।
(এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠক দেখতে পারেন অশোক সেনের লেখা প্রবন্ধ “আধুনিকের সীমানায় বিদ্যাসাগর”, আকাদেমি পত্রিকা ৬-এর অন্তর্গত)
পরিশেষে আসা যাক বর্তমান ভারতে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কাজের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে। কীভাবে এবং কেন বিদ্যাসাগর আজকের হিন্দু রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের প্রেরণা?
২০১৯এর লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর রোড শো চলাকালীন বিদ্যাসাগর মূর্তি ভেঙে দেবার যে ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল এবং মুখ বাঁচাতে শেষপর্যন্ত বিজেপি যাকে নিজেদের কাজ বলতে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়, তার পেছনের কারণটা বোঝা কঠিন নয়। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচনার জায়গা স্বাভাবিকভাবেই বেশ বিস্তৃত। বিজেপি যখন যেখানে ক্ষমতায় এসেছে সেখানেই তারা পাঠ্যক্রমে ভারতের অতীত গৌরবকে স্মরণ করার নামে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনাকে অনেকাংশে কোতল করেছে এবং প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাসকে পুরাণ ও কল্পকথা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর যখন পাঠ্যক্রম নিয়ে কথা বলেন সেখানে সংস্কৃতের কৃতবিদ্য পণ্ডিত হয়েও তিনি অদ্বৈত বেদান্ত বা নব্যন্যায়ের মতো ভাববাদী দর্শনকে বাদ দিয়ে বাস্তববাদী দর্শনকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর ঐতিহ্য থেকে সরে আসার কথা কখনো বলেননি। সাহিত্যে কালিদাস বা ভবভূতি অবলম্বনে অনুসৃজন করেন তিনি। শকুন্তলা বা সীতার বনবাস বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশের দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সেটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই ক্ষেত্রেও গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মনন ছিল অত্যন্ত সতর্ক। রাম সীতার আখ্যান সেখানে আসে, কিন্তু কালিদাসের নাটকের ব্রাহ্মণ্য মহিমা কীর্তনের অংশটুকুকে বাদ দিতে বিদ্যাসাগর ভোলেন না। সংস্কৃত কলেজের দরজা অব্রাহ্মণদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া বা জীবনের উত্তরকাল কার্মাটাড়ে আদিবাসীদের এলাকায় কাটানো মানুষটি আসলে ঐতিহ্য আর আধুনিকতাকে উপযুক্ত বিন্যাসে মেলাতে জানতেন। ডিরোজিয়ানদের একপেশে বিদ্রোহ আর রক্ষণশীলদের অবস্থানের দ্বিতত্বের বাইরে নতুন গঠনমূলক সংস্কারক দৃষ্টিকোণই বিদ্যাসাগরের অবস্থানকে বিশিষ্টতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব দিয়েছে।
বিদ্যাসাগর শুধু নিরীশ্বরবাদীই ছিলেন না, বাংলার ইতিহাসে ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদকে বিকশিত করার লড়াইয়ে অন্যতম প্রথম যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর দুটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাক। “একথা অবশ্য মানতে হবে যে হিন্দু দর্শনের মধ্যে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে যাকে সহজে ও যথেষ্ট বোধগম্যরূপে ইংরাজিতে অনুবাদ করা যায় না। তার একমাত্র কারণ, তাদের মধ্যে সারবস্তু কিছুই নেই।” বস্তুবাদের প্রসার ঘটানোর জন্য পাঠ্যক্রমে কেমন ধরনের বিন্যাস তিনি চেয়েছিলেন তা বোঝা যাবে পরবর্তী উদ্ধৃতিটি থেকে। “বেদান্ত আর সাংখ্য যে দার্শনিক মত হিসেবে ভ্রান্ত, তা নিয়ে এখন আর কোনও সংশয় নেই। তবে যত ভ্রান্তই হোক, এই মতগুলির প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। সংস্কৃত ক্লাসে এইসব দর্শন পড়াতেই হবে, তাই এর পাল্টা হিসেবে, এদের প্রভাব দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ইংরাজি ক্লাসে এমন দর্শন পড়ানো উচিত, যা যুক্তির দিক থেকে মজবুত।”
(এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠক দেখতে পারেন আশীষ লাহিড়ীর লেখা বই “অন্য কোনও সাধনার ফল: বিজ্ঞান ও বাঙালি সংস্কৃতি” এবং বিনয় ঘোষের লেখা বই “বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ”)
আজকের ভারতে আমরা দেখি হিন্দুত্ববাদীরা ঐতিহ্য রক্ষার নামে তাদের কথাবার্তায় ও সাংগঠনিক আস্ফালনে যাবতীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কারকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। নারী পুরুষের স্বাভাবিক মেলামেশা ও নারীর স্বাধীন পছন্দর অধিকারকে কখনো তারা রোমিও স্কোয়াড আটকানোর নামে, কখনো লাভ জেহাদের নামে কোতল করে। বিদ্যাসাগর সেই রক্ষণশীলতার যুগে দাঁড়িয়ে যেভাবে প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেছিলেন বা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন – তাকে পুরুষতান্ত্রিক সামন্তী মানসিকতার হিন্দুত্ববাদিরা কিছুতেই খোলা মনে মেনে নিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা সংস্কারক ও ভাষা সংস্কারক বিদ্যাসাগরের পাশে উজ্জ্বল যে সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর, তাঁর গোটা সক্রিয়তাটাই প্রায় নারীর অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বিধবা বিবাহের সমর্থনে তাঁর অক্লান্ত লড়াই এবং এই সংক্রান্ত আইন পাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবাদ প্রতিম ভূমিকা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এমনকি সমকালে যে সমস্ত আন্দোলনকে আইনে রূপান্তরিত করতে সে সময় বিদ্যাসাগর রক্ষণশীলদের বাধায় সফল হননি, বহুবিবাহ প্রথার মতো সেই সমস্ত ব্যাপারেও তিনি নারী অধিকারের দিক থেকে অনেক প্রশ্ন তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়েসকে বাড়ানোর পক্ষে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখনও প্রচলিত গর্ভাধান প্রথার প্রসঙ্গ তুলে রক্ষণশীলরা তার বিরোধিতা করেছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু নারী রজস্বলা হবার আগে তার বিবাহের বিরুদ্ধে আইন পাশ করার ব্যাপারে তাঁর মতে দৃঢ় ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁর মূর্তি হিন্দুত্ববাদীদের কার্যকলাপ ও চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে এক জীবন্ত প্রতিবাদ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা এই প্রতিবাদের উত্তরাধিকার বহন করি। বিদ্যাসাগর হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে বাংলা ও দেশজোড়া লড়াইয়ের আমাদের অন্যতম প্রধান প্রেরণা হয়ে থাকেন।
- সৌভিক ঘোষাল